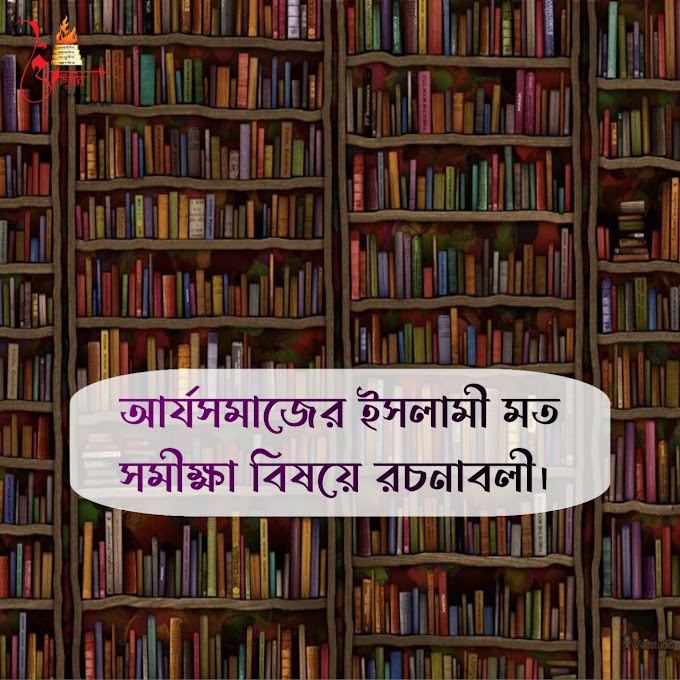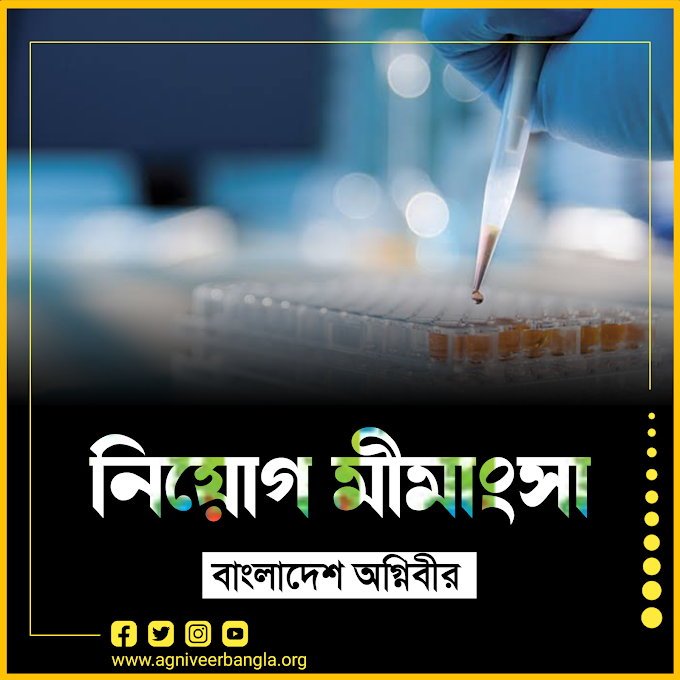অমৃতসরে পৌরাণিক পণ্ডিতবর্গ এবং শ্রীশঙ্করাচার্যের সাথে নয় ঘণ্টার মহান শাস্ত্রার্থ
[পৌরাণিক পণ্ডিতবর্গ এবং শ্রী গোবর্ধনপীঠাধীশ শঙ্করাচার্য বা শ্রী স্বামী করপাত্রীজির সাথে অমৃতসরে আমার ১৬, ১৭ নভেম্বর মোট ৬.৫ ঘণ্টা সংস্কৃতে এবং ২.৫ ঘণ্টা হিন্দিতে শাস্ত্রার্থ হয়েছিল। যদিও এই শাস্ত্রার্থ ছিল আমার ব্যক্তিগত, তবুও যেহেতু আমি ঋষি দয়ানন্দ প্রদর্শিত বৈদিক সিদ্ধান্তগুলিতে পূর্ণ আস্থা রাখি, তাই এই শাস্ত্রার্থ আর্যসমাজের সাথে হয়েছিল বলেই গণ্য করা হয়েছিল। এই শাস্ত্রার্থের কথা উল্লেখও আমাকেই করতে হচ্ছে, যা আমার স্বভাবের বিরোধী। তবে, এই শাস্ত্রার্থে এমন অনেক আজ পর্যন্ত অনুচ্চারিত প্রমাণ, সেগুলির গভীর অর্থ এবং যুক্তি পেশ করা হয়েছিল, যা আর্য-জনতা এবং আর্য পণ্ডিতবর্গের জন্য ভবিষ্যতে কখনো লাভপ্রদ হতে পারে (বিশেষত ১৭ তারিখের মধ্যাহ্নের পরের শাস্ত্রার্থের সময়কার)। তাই, অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি এই শাস্ত্রার্থের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা উপস্থিত করছি। এতে এমন একটি শব্দও নেই যা সেই সময়ের বর্ণনা থেকে বাইরের। হ্যাঁ, ভাষান্তর অবশ্যই করা হয়েছে। এটি 'বেদবাণী'-তে দ্রুত প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু পূজ্য গুরুদেবের মহাপ্রয়াণের কারণে সময়মতো প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। ]
— যুধিষ্ঠির মীমাংসক
সম্মেলনের পটভূমি
অমৃতসরে ১১ নভেম্বর থেকে ১৯ নভেম্বর ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত অখিল ভারতবর্যীয় সর্ব বেদশাখা সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এর সভাপতি ছিলেন গোবর্ধন পীঠাধীশ (পুরীর শঙ্করাচার্য) এবং শ্রী করপাত্রীজির সভাপতিত্বে হয়েছিল। প্রায় ৫০ জন বৈদিক তথা অন্যান্য বিষয়ের পণ্ডিত এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সম্মেলনের পক্ষ থেকে প্রায়শই কয়েকজন আর্য পণ্ডিতকে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং যাতায়াত খরচ দেওয়ার ব্যবস্থাও সম্মেলন কর্তৃপক্ষই করে।
আমিও প্রায় সর্বদা নিমন্ত্রণ পেয়ে থাকি। চার বছর আগে দিল্লির অধিবেশনে আমি যোগদান করেছিলাম এবং এবার পুনরায় যোগদানের সুযোগ পেলাম।
দিল্লির অধিবেশনে, শেষ দিন মধ্যাহ্নে সভাপতি শ্রী করপাত্রীজি উঠে যাওয়ার পর, একজন পৌরাণিক বক্তা আর্যসমাজ এবং ঋষি দয়ানন্দের বিরুদ্ধে যথেষ্ট অনুপযুক্ত কথা বলেন। মধ্যাহ্নের পর সভা শুরু হলে, আমি শ্রী করপাত্রীজির অনুপস্থিতিতে ঘটা সেই অন্যায় কার্যকলাপের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে শ্রী স্বামী মেধানন্দনী সরস্বতীজির মাধ্যমে পৌরাণিক বক্তা কর্তৃক বলা অনুপযুক্ত কথাগুলির উত্তর দেওয়ার ব্যবস্থা করাই। অতঃপর, আমি ঋষি দয়ানন্দের বেদভাষ্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটি বিশেষ বক্তৃতা দিই। উপরোক্ত আকস্মিক ঘটনাটি ছাড়া দিল্লির অধিবেশনের কার্যক্রম প্রায় সংযতভাবে চলেছিল। পণ্ডিতদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে।
এইবার শ্রী শঙ্করাচার্যজির কাছ থেকে আমন্ত্রণ পাওয়ায় আমি তাঁকে একটি চিঠি লিখি, যেখানে দিল্লিতে ঘটা অনুপযুক্ত ঘটনার ইঙ্গিত করি এবং লিখি যে, যখন আপনারা আপনাদের থেকে ভিন্ন মতের পণ্ডিতদেরও সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানান, তখন তাঁদের মতবাদগুলির প্রতিও মনোযোগ দেওয়া আপনাদের কর্তব্য। যদি আমাদের ডেকে এনে আমাদের সামনে ঋষি দয়ানন্দ এবং আর্যসমাজ সম্পর্কে অসংযত প্রলাপ করা হয়, তবে তার একমাত্র অর্থ এটাই হবে যে আমাদের ডেকে অপমান করার আপনাদের পরিকল্পনা রয়েছে। যদি তা-ই হয়, তবে আমাদের আসা অর্থহীন। আমি তো কেবল শাস্ত্রীয় আলোচনাতেই অংশগ্রহণ করতে চাই। ইত্যাদি।
এই চিঠির যে উত্তর আসে, তার প্রথমাংশ প্রায় প্রতিক্রিয়াশীল কথায় পূর্ণ ছিল, কিন্তু শেষে লেখা ছিল যে, আপনারা বিশ্বাস রাখুন, এমন কোনো অনুপযুক্ত কার্যকলাপ হবে না। আপনারা আসতে চাইলে আসতে পারেন।
যেহেতু অমৃতসরে আমার আরও কিছু কাজ ছিল, তাই আমি উত্তর দিই যে আমি ১৫ নভেম্বর মধ্যাহ্নের পর পৌঁছাব। সেই অনুযায়ী, আমি ১৫ নভেম্বর সন্ধ্যা ৫টায় সম্মেলনে উপস্থিত হই।
আর্যসমাজের ঔদাসীন্য
এবারের সম্মেলনে, হয় আমার চিঠির কারণে অথবা তার পূর্বে অমৃতসরের আর্যসমাজের উৎসবে আর্যসমাজের পক্ষ থেকে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলির জন্য ক্ষুব্ধ হওয়ার কারণে, আর্যসমাজকে ছোট করার একটি সম্ভাব্য পরিকল্পনা সম্ভবত আগে থেকেই তৈরি রাখা হয়েছিল। এ বিষয়ে আমার কিছুই জানা ছিল না।
অমৃতসর শহরে আর্যসমাজের ভালো প্রভাব রয়েছে। তাদের সামনেই এই মহান আয়োজনের প্রস্তুতি অনেক দিন ধরে চলছিল। স্বয়ং শঙ্করাচার্য মহাশয় তিন মাস ধরে সেখানে অবস্থান করছিলেন, তবুও অমৃতসর আর্যসমাজের নেতারা এই সম্ভাব্য আক্রমণের প্রতিরোধের জন্য কোনো চেষ্টা করেননি। ১১ বা ১২ তারিখে কেবল সার্বদেশিক সভাকে শাস্ত্রার্থের জন্য পণ্ডিতদের পাঠাতে তার পাঠিয়ে নিজেদের কর্তব্য শেষ বলে মনে করেছিলেন।
দিল্লির অধিবেশনেও একই পরিস্থিতি ছিল। সার্বদেশিক সভা এবং স্থানীয় প্রায় ১১০টি সমাজ থাকা সত্ত্বেও, কেউই প্রয়োজনের সময় উপযুক্ত উত্তর দেওয়ার জন্য দু-চারজন পণ্ডিতকে ডেকে প্রস্তুত রাখেননি। সেই অধিবেশনে শ্রী পণ্ডিত বুদ্ধদেবজি এবং শ্রী স্বামী রামেশ্বরানন্দজি কিছু সময়ের জন্য ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত ছিলেন। বস্তুত, আর্যসমাজের এই ঔদাসীন্য তার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক হচ্ছে এবং বিরোধীদের মনোবল অনেক বেড়ে গেছে।
শাস্ত্রার্থের সূচনা
১৬ নভেম্বর প্রাতে আমি ১০টায় অধিবেশনে উপস্থিত হই। আমাকে দেখে একজন পৌরাণিক পণ্ডিত (পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে) উঠে বললেন:
[১] "বেদে বিজ্ঞান আছে কি নেই"- এই বিষয়ে এখন শাস্ত্রার্থ হবে। আমাদের পক্ষ হলো যে, বেদে বিজ্ঞান নেই, বেদ কেবল যজ্ঞকর্মের জন্য। তাই, যাজ্ঞিক অর্থই প্রামাণিক। স্বামী দয়ানন্দ আধুনিক বিজ্ঞান দেখে সেই অনুযায়ী বেদ থেকে বিজ্ঞান বের করার চেষ্টা করেছেন।
উদাহরণস্বরূপ- ‘আয়ং গৌঃ পৃশ্নিরক্রমীৎ’ মন্ত্র থেকে পৃথিবীর সূর্যের চারপাশে ঘোরাকে সিদ্ধ করেছেন, অথচ বেদের সিদ্ধান্ত হলো সূর্য ঘোরে। যে কেউ বেদে বিজ্ঞান মানে, সে স্বামী দয়ানন্দের অর্থের প্রামাণিকতা সিদ্ধ করুক। [২]
[পাদটীকা ১. মনে রাখবেন যে, সম্মেলনের সমস্ত কার্যক্রম প্রায় সংস্কৃতেই হয়েছিল। তাই শাস্ত্রার্থও সংস্কৃতেই হয়েছিল।]
[পাদটীকা ২. মনে রাখবেন যে, পূর্বপক্ষ প্রধান বিষয়ের প্রতিপাদন না করে ঋষি দয়ানন্দের মন্ত্রার্থের উপর সরাসরি আপত্তি করেছিলেন, কেবল আমাকে শাস্ত্রার্থে টানার জন্য।]
যদিও এটি আমাকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছিল, তবুও এই আশায় যে, সম্ভবত স্থানীয় আর্যসমাজের লোকেরা অন্য কোনো পণ্ডিতের ব্যবস্থা করে রেখেছেন এবং তাঁরা এসেছেন, তা ভেবে আমি নীরব রইলাম। এক মিনিট পর পুনরায় ঘোষণা করা হলো যে, যে কেউ স্বামী দয়ানন্দের উপস্থাপিত মন্ত্রার্থের প্রামাণিকতা সিদ্ধ করতে চান, তিনি করুন, অন্যথায় এটি ধরে নেওয়া হবে যে স্বামী দয়ানন্দের উক্ত মন্ত্রার্থ অশুদ্ধ।
এই দ্বিতীয় ঘোষণায় আমি উঠলাম। উঠে বললাম যে, বেদে বিজ্ঞান আছে, শুধু তাই নয়, বিজ্ঞানই বেদের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। ভারতীয় বিজ্ঞান এবং ইউরোপীয় বিজ্ঞানের মধ্যে আকাশ-পাতালের পার্থক্য এবং ইউরোপীয় বিজ্ঞান প্রায়শই পরিবর্তিত হতে থাকে। অতএব, যে ব্যক্তি আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অনুসারে বেদ থেকে বিজ্ঞান বের করার চেষ্টা করে, সে বস্তুত নিন্দনীয়, কিন্তু স্বামী দয়ানন্দ বেদার্থে যে পৃথিবী ভ্রমণের বিজ্ঞানের প্রতিপাদন করেছেন, তা ভারতীয় বিজ্ঞান। আর্যভট্ট তাঁর সিদ্ধান্ত শিরোমণি গ্রন্থে পৃথিবী ভ্রমণের বিস্তারিত প্রতিপাদন করেছেন। ঐতরেয় এবং গোপথ ব্রাহ্মণ-এ সূর্যের উদয় ও অস্ত হওয়ার নিষেধ করা হয়েছে। এতে স্পষ্ট যে, প্রাচীন ভারতীয় ঋষি, মুনি এবং আচার্যরা পৃথিবী ভ্রমণকে তাত্ত্বিকভাবে মানতেন।*[৩] যেখানে যেখানে সূর্য ভ্রমণের উল্লেখ প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে রয়েছে, তা স্থূল দৃষ্টিতে করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, সম্পূর্ণ শ্রৌত যজ্ঞ বিজ্ঞানমূলক; এগুলি সৃষ্টির উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয়কালে ঘটা আধিদৈবিক যজ্ঞের রূপক (এই প্রসঙ্গে কর্মকাণ্ডগত অগ্ন্যাধানের পার্থিব অগ্নিতে আধানের রূপকত্ব প্রাচীন সংহিতা এবং ব্রাহ্মণ গ্রন্থ থেকে বিস্তারিতভাবে বলা হলো)। এই কারণে, যখন কর্মকাণ্ডগত যজ্ঞ মূলত আধিদৈবিক বিজ্ঞান-মূলক, তখন বেদের যাজ্ঞিক অর্থের পরিসমাপ্তিও আধিদৈবিক বিজ্ঞানেই হয়। তাই, বেদের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় বিজ্ঞানই। একই সাথে, এটাও মনে রাখতে হবে যে, ভারতীয় পরম্পরায় এটি সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত যে বেদের প্রতিটি মন্ত্রের অর্থ তিন প্রকারের হয়, যথা- যাজ্ঞিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক (এতে স্কন্দ স্বামী প্রমুখের অনেক প্রমাণ দেওয়া হলো)। আধিদৈবিক অর্থ সম্পূর্ণ বিজ্ঞানমূলকই। অতএব, বেদের বৈজ্ঞানিক অর্থ করা বস্তুত ঠিক।
[পাদটীকা ৩. এই বিষয়ে যে মহানুভাবরা বিস্তারিত জানতে চান, তাঁরা ঋষি দয়ানন্দ কৃত যজুর্বেদ ভাষ্যের আমার গুরুদেব শ্রী পণ্ডিত ব্রহ্মদত্তজি জিজ্ঞাসু কৃত ভাষ্য বিবরণ অ. ৩ ম. ৬ পৃষ্ঠা ২৪৯-২৫৬ পর্যন্ত দেখুন।]
আমার এই স্থাপনার পর, পূর্বপক্ষীয় পণ্ডিত প্রধান বিষয় ছেড়ে দিয়ে মন্ত্রের অর্থ তিন প্রকারের হয় কি না, এই বিষয়েই জোর দিলেন এবং পূর্বাহ্নের পুরো সময় এই বিষয়েই ব্যয় হলো। অবশেষে, শঙ্করাচার্য মহাশয় আমাকে বললেন যে, "আপনি তিন প্রকারের অর্থ হয়, বারবার বলছেন; কোনো একটি মন্ত্রের তিন প্রকারের অর্থ করে দেখান, ‘অগ্নিমীলে’-এরই করুন।" যেহেতু এই প্রশ্নটি প্রায় একটার সময় করা হয়েছিল, সভা শেষ হওয়ার পথে ছিল; তাই আমি বললাম যে, কাল সকালে আমি উক্ত মন্ত্রের তিন প্রকারের অর্থ বলবো। [৪] এরপর সভা সমাপ্ত হলো।
[পাদটীকা ৪. কাজের কারণে আমাকে মধ্যাহ্নের পর উপস্থিত থাকার কথা ছিল না।]
১৭ তারিখে প্রাতে ঠিক ১০টায় আমি সম্মেলনে উপস্থিত হলাম এবং দাঁড়িয়ে পূর্ব প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী ‘অগ্নিমীলে’ মন্ত্রের ত্রিবিধ ব্যাখ্যা শুরু করলাম। কিছু সময় পর, জনতার পক্ষ থেকে হিন্দিতে কথা বলার জন্য আওয়াজ আসতে শুরু হলো। সভাপতি শ্রী শঙ্করাচার্যজি আমাকে বললেন যে, আপনার পক্ষের লোকেরা কোলাহল করছে, এদের শান্ত করুন। এর উত্তরে আমি বললাম যে, আমার পক্ষ থেকে এখানে কেউ নেই, কারণ আমাকে এখানকার কোনো ব্যক্তি ডাকেননি। আপনার আমন্ত্রণে এসেছি। অতএব, যারা কোলাহল করছেন, তারা সবাই আপনারই পক্ষের।
এইভাবে, অবশেষে কার্যক্রম হিন্দিতে শুরু হলো। আমি যজ্ঞীয় মন্ত্রার্থ, যা উভয় পক্ষ দ্বারা সম্মত ছিল, তা করে তারই ভিত্তিতে আধিদৈবিক ব্যাখ্যা করলাম। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা পুরোপুরি উপস্থিত করিনি, তার আগেই বেশি সময় হয়ে যাওয়ার অজুহাতে সভাপতির আদেশে আমাকে বসতে হলো। এরপর পূর্বপক্ষীয় পণ্ডিত পুনরায় তাঁদের কৌশল বদলালেন। ব্রাহ্মণ গ্রন্থ বেদ কি না, এই বিষয়ে প্রশ্ন করলেন। পূর্বাহ্নে সমস্ত বাদানুবাদ এই বিষয়েই চলতে থাকল।
এই প্রসঙ্গে আমি বললাম যে, যে ‘মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্’ বচন অনুসারে ব্রাহ্মণের বেদ-সংজ্ঞা মানা হয়, সেই বচন কেবল কৃষ্ণ যজুর্বেদের শ্রৌত সূত্রগুলিতেই পাওয়া যায়। ঋগ্বেদ, শুক্ল যজুর্বেদ এবং সামবেদের শ্রৌত সূত্রগুলিতে নেই। এর কারণ এই যে, ঋগ্বেদ, শুক্ল যজুর্বেদ এবং সামবেদের মন্ত্র সংহিতাগুলি স্বতন্ত্র এবং এদের ব্রাহ্মণগুলি স্বতন্ত্র ও পৃথক, কিন্তু কৃষ্ণ যজুর্বেদের সংহিতাগুলিতে (শাখাগুলিতে) মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ উভয়ের সম্মিশ্রণ রয়েছে। অতএব, প্রাচীন পরম্পরা অনুসারে তাদের একটি অংশ মন্ত্রেরই বেদ-সংজ্ঞা প্রাপ্ত ছিল, ব্রাহ্মণ ভাগের নয়। [৫] এইভাবে সম্পূর্ণ সংহিতার বেদত্ব সিদ্ধ করার জন্যই কৃষ্ণ যজুর্বেদের শ্রৌতসূত্রকারদের এমন বচন তৈরি করতে হয়েছিল। সেই কারণেই এই সূত্রের ব্যাখ্যায় হরদত্ত এবং ধূর্ত স্বামী স্পষ্ট লিখেছেন ‘কৈশ্চিন্মন্ত্রাণামেব বেদত্বমাশ্রিতম্’ অর্থাৎ কোনো কোনো ব্যক্তি কেবল মন্ত্রেরই বেদত্ব স্বীকার করেছেন। এতেও স্পষ্ট যে, প্রাচীন অনেক আচার্য মন্ত্রকেই বেদ মানতেন, ব্রাহ্মণকে নয়। শুধু তাই নয়, যদি এই বচনটিকে প্রমাণও মানা হয়, তবুও এটি আপস্তম্বাদি শ্রৌত সূত্রগুলির সংজ্ঞা অংশে পঠিত হওয়ার কারণে তা পারিভাষিক সংজ্ঞা এমন মানতে হবে। পারিভাষিক সংজ্ঞা কেবল সেই শাস্ত্রেই স্বীকৃত হয়, যেখানে তা বলা হয়েছে। যেমন, পাণিনির ‘অ’, ‘এ’, ‘ও’ বর্ণের গুণ-সংজ্ঞা কেবল পাণিনীয় শাস্ত্রেই স্বীকৃত হবে। লোক বা ন্যায়াদি শাস্ত্রে গুণ শব্দ দ্বারা ‘অ’, ‘এ’, ‘ও’-কে গ্রহণ করা হবে না। অতএব, ‘মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্নামধেয়ম্’ সূত্র থেকে ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলির সাধারণভাবে বেদ-সংজ্ঞা হতে পারে না। আমি এই সূত্রের উপর পুরো বিস্তারিত বিচার ১২ বছর আগে ‘মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্নামধেয়ম্ ইত্যত্র কশ্চিদভিনবো বিচারঃ’ পুস্তিকায় উপস্থিত করেছি। শ্রী করপাত্রীজি (তিনি সেখানেই উপস্থিত ছিলেন) তার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করলেন, কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন না যে, কেন কেবল কৃষ্ণ যজুর্বেদীদেরই এমন সূত্র তৈরি করার প্রয়োজন হয়েছিল, ঋগ্বেদাদির শ্রৌত সূত্রকাররা কেন সূত্র তৈরি করেননি। কারণ স্পষ্ট। ঋগ্বেদাদিতে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের পূর্ণ পার্থক্য রয়েছে, সংমিশ্রণ নেই, তাই তাঁদের এমন বচন তৈরি করার প্রয়োজনই হয়নি, এর কোনো উত্তর তিনি দিলেন না। শুধু তাই নয়, আমার ঘোষণা যে, কোনো পৌরাণিক পণ্ডিত এই বিশ্লেষণের সঠিক উত্তর আকল্পান্ত (কল্পের শেষ পর্যন্ত) দিতে পারবেন না। এর সাথে ব্রাহ্মণ গ্রন্থের অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করা হলো, যা থেকে স্পষ্ট হয় যে ব্রাহ্মণ বেদ থেকে পৃথক। এইভাবে ১টার সময় এই প্রসঙ্গ শেষ হলো।
[পাদটীকা ৫. এখানে ব্রাহ্মণ ভাগে ‘ভাগ’ শব্দের প্রয়োগ কৃষ্ণ যজুর্বেদের সংহিতার দৃষ্টিতে করা হয়েছে। আর্যসমাজের অনেক পণ্ডিত প্রায়শই মন্ত্র ভাগ এবং ব্রাহ্মণ ভাগ শব্দ ব্যবহার করেন, যা ভুল, কারণ যদি মন্ত্র ভাগও বেদ হয়, যদি এমন বলা হয়, তবে তার দ্বিতীয় ভাগকেও বেদ মানতে হবে। যে বৃক্ষত্ব বৃক্ষের কিছু শাখায় আছে, তা তার অন্য শাখাগুলিতে এবং মূল বা কাণ্ডেও আছে। অতএব, মন্ত্র ভাগ বেদ, এমন স্বীকার করলে ব্রাহ্মণ ভাগকেও ন্যায়ের দৃষ্টিতে আপতত বেদ মানতে হবে। সুতরাং, মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণের সাথে ‘ভাগ’ শব্দের ব্যবহার ভুল করেও করা উচিত নয়।]
মধ্যাহ্নের পর পুনরায় ৩:৩০টা থেকে সংস্কৃতে শাস্ত্রার্থ শুরু হলো এবং শেষ পর্যন্ত সংস্কৃতেই চলতে থাকল।
প্রথমে আমি গোপথ ব্রাহ্মণ পৃ. ২।১০-এর বচন উপস্থিত করলাম—‘এবমিমে সর্বে বেদাঃ নির্মিতাঃ সকল্পাঃ সরহস্যাঃ সব্রাহ্মণাঃ সোপনিষৎকাঃ’ (এতটুকুই উপস্থিত করলাম, বাকিটা পরের বারের জন্য ছেড়ে দিলাম)। এই বচনে রহস্য অর্থাৎ আরণ্যক, ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদকে বেদ থেকে পৃথক করে গণনা করা হয়েছে। যদি এগুলি বেদের অন্তর্ভুক্তই হয়, তবে পৃথকভাবে গণনার কী প্রয়োজন? এতে স্পষ্ট যে, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ্ বেদ নয়। এমন প্রমাণ উপস্থিত করলে পৌরাণিক পণ্ডিতরা বলে থাকেন যে, যদিও ব্রাহ্মণ গ্রন্থ বেদের অন্তর্ভুক্ত, তবুও ‘ব্রাহ্মণ বসিষ্ঠ ন্যায়’-[৬] দ্বারা ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলির বৈশিষ্ট্য দেখানোর জন্য পৃথক নির্দেশ করা হয়েছে। পূর্বপক্ষীয় পণ্ডিত যেন এই কথা না বলেন, তাই আমি স্পষ্ট করে দিলাম যে, ব্রাহ্মণ বসিষ্ঠ ন্যায় সেখানেই লাগে, যেখানে বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই এটা মানেন যে বসিষ্ঠও ব্রাহ্মণ। যদি এদের মধ্যে একজনও এটা না জানে যে বসিষ্ঠও ব্রাহ্মণ, তবে এই ন্যায় লাগে না। এখানেও এই ন্যায় তখনই লাগতে পারে, যখন উভয় পক্ষ স্বীকার করে নেয় যে ব্রাহ্মণ গ্রন্থও বেদ। কিন্তু ব্রাহ্মণ গ্রন্থ বেদ, এটা তো এখনও সাধ্য (প্রমাণ করার বিষয়)। শুধু তাই নয়, ‘সরহস্যাঃ সব্রাহ্মণাঃ সোপনিষৎকাঃ’-তে ‘স’ শব্দের প্রয়োগ রয়েছে। এর প্রয়োগ সর্বদা অপ্রধানের সাথেই হয়, যেমন ‘দেবদত্তঃ সপুত্রঃ সমাগতঃ’ (দেবদত্ত পুত্রসহ এলেন) –এখানে দেবদত্তের আগমন মুখ্য, পুত্রের গৌণ। তাই এই বচনে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদকে পৃথক স্বীকার করেও (যেমন দেবদত্ত এবং তাঁর পুত্র পৃথক) বেদ থেকে এদের হীনতা বা অপ্রধানতাই ব্যক্ত করা হয়েছে।
[পাদটীকা ৬. ‘ব্রাহ্মণা আয়াতাঃ বসিষ্ঠোঽপ্যায়াতঃ’ (ব্রাহ্মণরা এসেছেন, বসিষ্ঠও এসেছেন)। এখানে বসিষ্ঠ ব্রাহ্মণ হওয়ায় ‘ব্রাহ্মণাঃ আয়াতাঃ’ বললেই কাজ চলে যেত, তবুও বসিষ্ঠের পৃথক নির্দেশ এই কারণে করা হলো যে, তিনি অন্য ব্রাহ্মণদের থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, প্রধান।]
এর উপর পূর্বপক্ষীয় বক্তা যথাযথ উত্তর না দিয়ে এদিক-ওদিকের কথা বলে নিজের সময় ব্যয় করলেন। এরপর আমি পুনরায় বললাম যে, পূর্ববর্তী আপত্তিগুলির কোনো সমাধান করা হয়নি, এর সাথে উক্ত বচনে পরে বলা হয়েছে- ‘সেতিহাসাঃ সপুরাণাঃ’ আপনার মতে (আমাদের মতে নয়) যে ইতিহাস (মহাভারত) এবং পুরাণ ব্যাস কৃত, সেগুলি কি বেদ? যেমন ব্রাহ্মণ গ্রন্থাদি। কারণ, এগুলিও একইভাবে স্মরণ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, অপৌরুষেয় বেদে (আপনার মতে) গোপথে ব্যাস নির্মিত মহাভারত বা পুরাণগুলির নির্দেশ কীভাবে হলো?
এর উপর পূর্বপক্ষীয় পণ্ডিত বললেন যে, প্রতিটি দ্বাপর যুগে ব্যাসজি পুরাণগুলির রচনা করেন, অতএব এই কর্ম প্রবাহ থেকে নিত্য, যেমন সূর্য, চন্দ্রাদির নির্মাণ। এর উপর আমি বললাম যে, আপনার পুরাণগুলিতে এটা লেখা নেই যে প্রতিটি দ্বাপরে ব্যাসজি পুরাণগুলির প্রবচন করেন, বরং বেদগুলির প্রবচন করেন– এতটুকুই লেখা আছে, অতএব আপনার উক্ত কথা ঠিক নয়। একই সাথে আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে, ‘মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্’ বচন থেকে তো ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলির বেদ-সংজ্ঞা হতে পারে না, এমন কোনো লক্ষণ (সংজ্ঞা) বলুন, যা দ্বারা ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিও বেদ বলে গণ্য হয়।
এর উপর পূর্বপক্ষীয় পণ্ডিত বললেন যে, ‘সম্প্রদয়া বিচ্ছিন্নত্বে সতি অস্মর্যমাণকর্তৃত্বং বেদত্বম্’ অর্থাৎ গুরু পরম্পরার বিচ্ছেদ না হওয়া সত্ত্বেও যে গ্রন্থের কর্তা স্মৃত নন (জানা নেই), তা বেদ। এতে যেমন মন্ত্রগুলির কর্তা স্মৃত নন, তেমনই ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলির কর্তা স্মৃত না হওয়ায় উভয় সমানভাবে বেদ।
পূর্বপক্ষীয় পণ্ডিতের এই লক্ষণের উপর ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলির লেখকদের নাম উপস্থিত করা যেত, কিন্তু তা না করে আমি তাঁদের লক্ষণের মধ্যেই ক্রমান্বয়ে দুটি দোষ উপস্থিত করলাম।
(১) আপনার মতে, যে গ্রন্থগুলির গুরু-শিষ্য সম্প্রদায় নষ্ট হয়নি, সেগুলি বেদ। আমরা আপনাদের গ্রন্থ থেকে জানি যে, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ্ গ্রন্থগুলি পূর্বে সস্বর ছিল, এখন শতপথ এবং তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ছাড়া সবই স্বর-রহিত হয়ে গেছে। অতএব, স্বরের লুপ্ত হওয়ায় স্পষ্ট যে, এই ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলির পঠন-পাঠনে গুরু-শিষ্য সম্প্রদায়ের নাশ হয়েছে। কারণ, যেখানে যেখানে গুরু-শিষ্য সম্প্রদায়ের নাশ হয়নি, সেই গ্রন্থগুলিতে অক্ষর, মাত্রা, বর্ণের একটিও পাঠান্তর পাওয়া যায় না, যেমন- শাকল সংহিতা, মাধ্যন্দিন সংহিতা, তৈত্তিরীয় সংহিতা ইত্যাদি। যে ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে স্বর লুপ্ত হয়ে গেছে, সেই লোপ সম্প্রদায় ভঙ্গ ছাড়া হতে পারে না, অতএব যে ব্রাহ্মণগুলির স্বর নাশ হয়েছে অর্থাৎ সম্প্রদায় ভঙ্গ হয়েছে, সেগুলি আপনাদের লক্ষণ অনুসারেই বেদ হতে পারে না।
এই অভূতপূর্ব কড়া আঘাতে সব পূর্বপক্ষীয় পণ্ডিত ঘাবড়ে গেলেন। পূর্বপক্ষীয় পণ্ডিত পরাজয় থেকে বাঁচার জন্য স্ব-মতের বিরুদ্ধে ‘স্বর-রহিত গ্রন্থও বেদ’—এই মত স্বীকার করলেন। এর উপর আমি শ্রী শঙ্করাচার্যজির কাছে ব্যবস্থা (সিদ্ধান্ত) চাইলাম যে, যদি ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি থেকে স্বর সরিয়ে দেওয়া হয়, তবে কি আপনি সেগুলিকে বেদ মানবেন? তাঁর কাছেও কোনো উত্তর ছিল না, তাই তিনি স্বীকার করলেন যে স্বর-রহিত মন্ত্রও বেদই। এর উপর আমি বললাম যে, আপনার এই কথা ঠিক নয়।*[৭] স্বর-রহিত গ্রন্থ কখনোই বেদ হতে পারে না, কারণ মীমাংসার কল্প সূত্রাধিকরণে ‘কল্পসূত্র বেদ কি না’ এই বিষয়ে বিচার করার সময়, তাদের বেদত্ব দূর করার জন্য যুক্তি দেওয়া হয়েছে ‘অসন্নিবন্ধনত্বাৎ’। এর টীকাকাররা অর্থ করেছেন ‘স্বররহিতত্বাৎ’ মানে স্বর-রহিত হওয়ার কারণে কল্পসূত্র বেদ নয়। এতে স্পষ্ট যে, স্বর-রহিত ব্রাহ্মণ গ্রন্থ বেদ হতে পারে না। এই প্রসঙ্গে আমি বললাম যে, প্রথম থেকেই সেই ব্রাহ্মণগুলিতে স্বর ছিল না – এটাও আপনি বলতে পারেন না, কারণ আগে লৌকিক ভাষাও সস্বর ছিল। পাণিনির বিভাষা ভাষায়াম্ (৬।১) সূত্র এতে প্রমাণ। এর উপর শ্রী শঙ্করাচার্য বলতে লাগলেন যে, পাণিনি স্বর-প্রক্রিয়ায় সমস্ত উদাহরণ বেদের দিয়েছেন। লৌকিক ভাষাতেও স্বর থাকলে তারও উদাহরণ দিতেন। শ্রী শঙ্করাচার্যের বক্তব্যের উত্তরে আমি বললাম যে, পাণিনি তাঁর অষ্টাধ্যয়ী-তে কোনো উদাহরণ দেননি। যে উদাহরণগুলি পাওয়া যায়, সেগুলি কাশিকার বামনের এবং সিদ্ধান্তকৌমুদীতে ভট্টোজী দীক্ষিতের। শুধু তাই নয়, আপনি আপনার কৌমুদী গ্রন্থ পাঠান, আমি পঞ্চাশো সূত্রের এমন উদাহরণ দেখাবো, যা বেদের নয়, লৌকিক ভাষার। এর উপর শ্রী শঙ্করাচার্যজি, যিনি নিজেকে মহাবৈয়াকরণ (মহান ব্যাকরণবিদ) মনে করেন, নিরুত্তর হতে বাধ্য হলেন।
[পাদটীকা ৭. এখান থেকে প্রায় মধ্যস্থ স্বরূপ শ্রী শঙ্করাচার্যজির সাথেই বাদানুবাদ হতে থাকল।]
(২) এরপর পূর্বপক্ষীয় পণ্ডিতের বেদের লক্ষণের দ্বিতীয় অংশের উপর দ্বিতীয় দোষ উপস্থিত করলাম। সম্প্রদায়ের নাশ না হওয়া সত্ত্বেও এমন অনেক গ্রন্থ আছে, যার কর্তার জ্ঞান আমাদের নেই, কিন্তু সেগুলি বেদ বলে গণ্য হয় না। যেমন মাধ্যন্দিন সংহিতার পদপাঠ। ঋগ্বেদের পদপাঠের কর্তা বা প্রবক্তা শাকল্য ছিলেন, সামবেদের গার্গ্য, অথর্বের শৌনক, তৈত্তিরীয়ের আত্রেয়। এমন মাধ্যন্দিন পদপাঠের কর্তা কে, তা কারও জানা নেই এবং এর গুরু-শিষ্য সম্প্রদায়ের নাশও হয়নি। যদি সন্দেহ হয়, তবে নিজের বৈদিকদের জিজ্ঞাসা করে নিন। অতএব, আপনার লক্ষণ অনুসারে এই পদপাঠও অপৌরুষেয় বেদ হবে, কিন্তু পদপাঠকে অপৌরুষেয় নিত্য মানা হয় না। অতএব, আপনার লক্ষণ উভয়ভাবে দোষযুক্ত হওয়ায় ত্যাজ্য।
এর উপরও পূর্বপক্ষীয় পণ্ডিত পুনরায় পরাজয় থেকে বাঁচার জন্য স্ব-মতের বিপরীত পদপাঠকেও নিত্য অপৌরুষেয় বেদ স্বীকার করলেন। এর উপর আমি পুনরায় মধ্যস্থ শ্রী শঙ্করাচার্যজির কাছে ব্যবস্থা (সিদ্ধান্ত) চাইলাম। শ্রী শঙ্করাচার্য এবং শ্রী করপাত্রীজি দুজনেই পদপাঠকে বেদ স্বীকার করলেন।
এই স্ব-পক্ষ-বিরুদ্ধ মত স্বীকার করায় আমি বিশেষভাবে শ্রী শঙ্করাচার্য এবং করপাত্রীজির সাথেই সরাসরি বিতর্কে নামলাম এবং পদপাঠ অনিত্য এবং পৌরুষেয়, এই কথা সিদ্ধ করার জন্য একটার পর একটা প্রমাণের ক্রমান্বয়ে ঝাঁক (প্রবাহ) লাগিয়ে দিলাম। সবার প্রথমে যাস্কের ‘বনেন বায়ো ন্যধায়ি চকন’ মন্ত্রের ব্যাখ্যায় শাকল্য কৃত পদপাঠের সম্বন্ধে লেখা বচন ‘বা ইতি চ য ইতি চ চকার শাকল্যঃ উদাত্তং ত্বেষমাখ্যাতমভবিষ্যৎ অসূসমাপ্তশ্চার্থঃ’ (‘বায়ো’-কে শাকল্য ‘বা যঃ’ দুটি পদ মেনে দু’টুকরো করেছেন, এমন করলে যত্-এর যোগ হওয়ায় অধায়ি ক্রিয়া উদাত্ত হওয়া উচিত, কিন্তু বেদে অনুদাত্ত এবং যত্-এর নির্দেশ দ্বারা মন্ত্রার্থও পূর্ণ হয় না যতক্ষণ না তত্-এর অধ্যাহার করা হয়) উপস্থিত করে বললাম যে, যাস্ক শাকল্য কৃত পদপাঠকে কেবল অনিত্যই মনে করেন না, বরং তাতে দোষও উপস্থিত করেন (দর্শান)। এর উপর মধ্যস্থ নিঘন্টু এবং উক্ত মন্ত্রের ঠিকানা জানতে চাইলেন। স্থান নির্দেশ করার পর অনেক পণ্ডিত উক্ত গ্রন্থগুলি বের করে পাতা ওল্টাতে লাগলেন। প্রায় ১০ মিনিট পরে করপাত্রীজি এর সমাধান করার চেষ্টা করলেন যে, যাস্কের ‘চকার’-এর অর্থ বানানো নয়, প্রবচন করা। ব্যাকরণ অনুসারে তো বেদের অনেক পদ অশুদ্ধ বলা যেতে পারে, কিন্তু সেগুলিকে কেউ অশুদ্ধ মানে না। অতএব, অর্থের দৃষ্টিতে ‘বায়োঃ’ একটি পদই, কিন্তু অধ্যয়নের ফলস্বরূপ অদৃশ্য (অদৃষ্ট) লাভের জন্য ‘বা যঃ’ এমনটাই পরম্পরাগতভাবে স্বীকার করা হয়। ইত্যাদি।
এর উপর আমি উত্তর দিলাম যে, যদি অর্থের দৃষ্টিতে ‘বায়োঃ’ দুটি পদযুক্ত না হয়, তবে যাস্কের শাকল্যের উপর দোষ দেওয়া এবং তাঁকে পৌরুষেয় বলা ঠিক। অন্যথায়, যদি আপনি পদপাঠকে অপৌরুষেয় নিত্য মানেন, তবে বলে দিন যে যাস্কের দোষ-দর্শন ভুল, আমি বসে যাব। শুধু তাই নয়, এখন আমি অন্য প্রমাণ দিচ্ছি, যাতে স্পষ্টত পদপাঠকে অনিত্য বলা হয়েছে, কৈয়ট মহাভাষ্য প্রদীপ ২।১।১০৯-এ লিখছেন, ‘সংহিতায়া এব নিত্যত্বং পদবিচ্ছেদস্য তু পৌরুষেয়ত্বম্’। অতএব, পদপাঠ অনিত্য পৌরুষেয়, এটা স্পষ্ট। এই কারণে পদপাঠ অপৌরুষেয় বেদ হতে পারে না।
এর উপরও করপাত্রীজি কৈয়টের বচন নিয়ে চিন্তা করে [৮] বলতে লাগলেন যে, বৈয়াকরণ বেদ বিষয়ে প্রমাণ নয়। কৈয়টের অনেক কথাকে নাগেশ খণ্ডন করে দিয়েছেন, অতএব কৈয়টের বচন প্রমাণ নয়।
[ পাদটীকা ৮. কৈয়টের বচনের পুরো ঠিকানা দেওয়ার পরও যখন দ্রুত পূর্বপক্ষীয়রা তা বের করতে পারলেন না, তখন মহাভাষ্য আমার কাছে পাঠানো হলো, আমি উক্ত পৃষ্ঠা বের করে তাঁদের দিলাম।
এর উপর আমি উত্তর দিলাম যে, যদিও নাগেশ কৈয়টের অনেক মতের খণ্ডন করেছেন, তবুও এই স্থানে খণ্ডন করেননি, অতএব এটা তাঁরও স্বীকৃত । শুধু তাই নয়, নাগেশ তো মহাভাষ্য ৬।৩-এর টীকায় পদপাঠগুলিতেও সম্প্রদায় ভ্রংশ মেনেছেন, যা না আপনি স্বীকার করেন, আর না আমি। এটাও মনে রাখতে হবে যে, যদি কৈয়ট পদপাঠগুলির পৌরুষেয়ত্বের বিধান স্বয়ং নিজের রূপে করে থাকতেন, তবে তাকে হয়তো কোনোভাবে অপ্রমাণ বলা যেত। কিন্তু কৈয়ট উক্ত মত তো মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির ‘ন লক্ষণেন পদকারা অনুর্ক্ত্যাঃ পদকারৈর্নাম লক্ষণমনুবর্ত্যম্’ (সূত্রকারকে পদকারদের অনুসরণ করা উচিত নয়, পদকারদের সূত্রকারদের লক্ষণের অনুসরণ করা উচিত) বচনের ব্যাখ্যায় লিখেছেন। মহাভাষ্যের উক্ত বচনের স্পষ্ট অর্থ এই যে, পদপাঠ পৌরুষেয় অনিত্য। যদি আপনি মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির বচনকেও বৈয়াকরণ হওয়ার কারণেই অপ্রমাণ বলেন, তবে আমি বসে যাব, এমন অবস্থায় আমার কিছু বলার নেই।
এর উপর পুনরায় কিছু সময় পরস্পর বিচার বিনিময় করে শ্রী করপাত্রীজি বললেন যে, মহাভাষ্যকারের উক্ত বচন প্রৌঢ়িবাদ মাত্র (একদেশী জোরপূর্বক উত্তর), সিদ্ধান্ত-স্বরূপ নয়। মহাভাষ্যকার অনেক স্থানে প্রৌঢ়িবাদ থেকে উত্তর দেন, সেই উত্তরগুলি প্রামাণিক বলে গণ্য হয় না।
এই বক্তব্যের উপর আমি বললাম যে, এটা সত্য যে মহাভাষ্যে প্রৌঢ়িবাদ থেকে অনেক উত্তর দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কোন্ উত্তর প্রৌঢ়িবাদ থেকে দেওয়া হয়েছে, তার জ্ঞানের জন্য দুটি কষ্টিপাথর (পরীক্ষার মানদণ্ড) রয়েছে। প্রথম- যে উত্তরের বিপরীত অন্য কোথাও লেখা পাওয়া যায়, সেই পরস্পর বিরোধী উত্তরগুলির মধ্যে একটি প্রৌঢ়িবাদের উত্তর হবে, দ্বিতীয়টি সিদ্ধান্ত-স্বরূপ। দ্বিতীয়- প্রৌঢ়িবাদের উত্তর একটি স্থানেই পাওয়া যাবে, তার পুনরায় পুনরায় নির্দেশ হবে না। সেই অনুসারে, পদপাঠ বিষয়ক উক্ত মতের বিরোধী বচন সম্পূর্ণ মহাভাষ্যে উপলব্ধ নয়, অতএব এটা প্রৌঢ়িবাদ থেকে বলা হয়েছে, এই কথা বলা অসত্য। শুধু তাই নয়, এই বচন মহাভাষ্যে অধ্যায় ৬ এবং ৮-এ আরও দুটি স্থানেও এসেছে। তাই অনেক স্থানে সমানভাবে বলা উত্তর প্রৌঢ়িবাদের বলে গণ্য হতে পারে না। এত কিছুর পরেও যদি বৈয়াকরণ হওয়ার কারণে মহাভাষ্যকারের বচনে সন্তোষ না হয়, তবে আমি বৈদিক বিদ্বানের মত উপস্থিত করছি, ভর্তৃহরি মহাভাষ্যের টীকায় ২৬৮ পৃষ্ঠায় লিখছেন, ‘এবং চ কৃত্বা বৃকো মাসকৃত ইত্যবগ্রহভেদোঽপি ভবতি। চন্দ্র মসি প্রবৃত্তো মাস শব্দো অবগৃহ্যতে বৃকে মাসকৃৎ’ (বৃকো মাসকৃত মন্ত্রে চন্দ্রমা অর্থে ‘মাস ऽকৃত্’ এমন একটি পদ মেনে অবগ্রহ করা হয় এবং বৃক অর্থে ‘মা স ऽকৃত্’ দুটি পদ মানা হয়)। যদি এটা বলা হয় যে, ভর্তৃহরির বচনও বৈয়াকরণ হওয়ার কারণে অপ্রমাণ, তবে তা অশুদ্ধ। ভর্তৃহরি বৈয়াকরণ হওয়া সত্ত্বেও পরম বৈদিক। তাঁর বৈদিকতা গণরত্নমহোদধিকার বর্ধমান-এর মতো জৈন আচার্যও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। বর্ধমান লিখেছেন- ‘তত্র ভবতাং বেদবিদামলংকারভূতেন ভর্তৃহরিণা’। যাস্কও বৈদিক। অতএব, যাস্ক, ভর্তৃহরি, পতঞ্জলি, কৈয়ট প্রমুখের উদ্ধৃত বচন থেকে স্পষ্ট যে, পদপাঠ গ্রন্থ অনিত্য পৌরুষেয়, এই পদপাঠ গ্রন্থ অপৌরুষেয় বেদ হতে পারে না। এইভাবে, আপনার বেদ লক্ষণ উভয়ভাবে দোষযুক্ত হওয়ায় ত্যাজ্য।
এরপর সাড়ে পাঁচটা বেজে যাওয়ায় শ্রী শঙ্করাচার্যজি তাঁর ভাষণে "এই শাস্ত্রার্থ জয়-পরাজয়ের জন্য করা হয়নি, জ্ঞানবর্ধনের জন্য করা হয়েছে, অতএব এখানে পরাজয়ের কোনো প্রশ্ন নেই, এখানে তো বাদ কথা হয়েছে। শ্রী মীমাংসকজি আমার পূর্বাশ্রমের মিত্রদের মধ্যে একজন, তাঁর যোগ্যতা আমি জানি। অত্যন্ত বিদ্বত্তা সহকারে তিনি তাঁর পক্ষের পোষণ করেছেন। এখন সময় বেশি হওয়ায় এই সভা সমাপ্ত করা হলো। পরের দিন জ্যোতিষ সম্মেলন হবে…..." ইত্যাদি বলে কোনোমতে তোড়জোড় করে সভা সমাপ্ত করলেন।
শ্রী শঙ্করাচার্যজির উক্ত ভাষণের মাঝখানে, যখন তিনি বাদ কথা-র নির্দেশ করলেন, তখন আমি মাঝখানে তাঁকে থামিয়ে বললাম যে, এই বাদানুবাদকে বাদ কথা বলা শাস্ত্রার্থের নিয়মের বিরুদ্ধ। আপনি দু’বার অস্থানে আমার জন্য নিগ্রহ স্থানের প্রয়োগ করেছিলেন, অর্থাৎ আপনি নিগ্রহ স্থানে চলে গিয়েছিলেন। সেই সময় আমি ইচ্ছাকৃতভাবে যে এই কথাটি ন্যায়শাস্ত্রে না চলে যায়, তাই কিছু বলিনি। কিন্তু আপনার জানা উচিত যে, বাদ কথায় প্রতিপক্ষের জন্য নিগ্রহ স্থানের প্রয়োগ হয় না। যেহেতু আপনি নিগ্রহ স্থানের প্রয়োগ করেছেন, অতএব আপনার বচন অনুসারেই এই কথা বাদ কথা না হয়ে জল্প বা বিতণ্ডা কথা ছিল, এটা প্রমাণিত হয়।
বিশেষ তথ্য
যখন থেকে পদপাঠের অনিত্যত্ব-এর প্রসঙ্গ শুরু হলো, সেই শেষ দেড় ঘণ্টায় ৩-৪ জন পৌরাণিক পণ্ডিত ক্রমাগত তাঁদের বইপত্র থেকে আমার দেওয়া উদ্ধৃতিগুলি বের করে শ্রী শঙ্করাচার্যজি এবং শ্রী করপাত্রীজির হাতে দিতে থাকলেন। তাঁরা দুজনে প্রতিবার ৫-১০ মিনিট চিন্তা করে উত্তর দিচ্ছিলেন। এতে সংস্কৃত থেকে অনভিজ্ঞ পৌরাণিক জনতাতেও আর্যসমাজের ভারী প্রভাব পড়ল। প্রায় অনেকেই বলতে শোনা গেল যে, "আর্যসমাজের পণ্ডিতটি খুব শক্তিশালী ছিল। সে একা মুখে মুখে ২-৩ মিনিটই বলত, আর তার উত্তর দেওয়ার জন্য অনেক পণ্ডিত একসাথে বইয়ের পাতা ওল্টাতেন এবং দুজনেই (শ্রী শঙ্করাচার্য এবং করপাত্রীজি) বই দেখে এবং ৫-৭ মিনিট ভেবে উত্তর দিতেন।"
এইভাবে, এই শাস্ত্রার্থের পৌরাণিক জনতার উপর তো ভারী প্রভাব পড়লই, কিন্তু অমৃতসরের আর্য-জনতাও বলতে লাগল যে, "আপনি আর্যসমাজের মান রক্ষা করেছেন।" আমি আর্যসমাজীদের উক্ত কথায় বললাম যে, "আপনারা এই বিশাল প্রস্তুতি দেখতে পেয়েও ঘুমিয়ে রইলেন। আমি তো সম্মেলনের দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলাম, আপনারা কী করলেন? আপনাদের এরকম ঔদাসীন্য আর্যসমাজকে নিয়ে ডুববে।"
এটিও জেনে রাখা উচিত যে, সমস্ত বিতর্কের বাদ-প্রতিবাদ টেপ রেকর্ডার মেশিন দ্বারা রেকর্ড করা হয়েছিল, কিন্তু অনেক সময় মেশিন বন্ধ হতো (মেশিনটি আমার কাছেই ছিল, তাই আমি দেখতে পাচ্ছিলাম)। যতদূর আমার মনে আছে, শেষ দৃশ্যটি তো রেকর্ড করাই হয়নি। এই লেখায় এক-দুটি স্থানে শ্রী করপাত্রীজি এবং শ্রী শঙ্করাচার্যজির নামের পরিবর্তন হতে পারে, কারণ প্রায় শেষ সময়ে দুজন মহানুভাবই উত্তর দেওয়ার জন্য প্রবৃত্ত হতেন।
॥ओ३म्॥
লেখক - মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যুধিষ্ঠির মীমাংসক
ভাষান্তর ও সম্পাদনা:
বিদুষামনুচরঃ
সুব্রত দেবনাথ