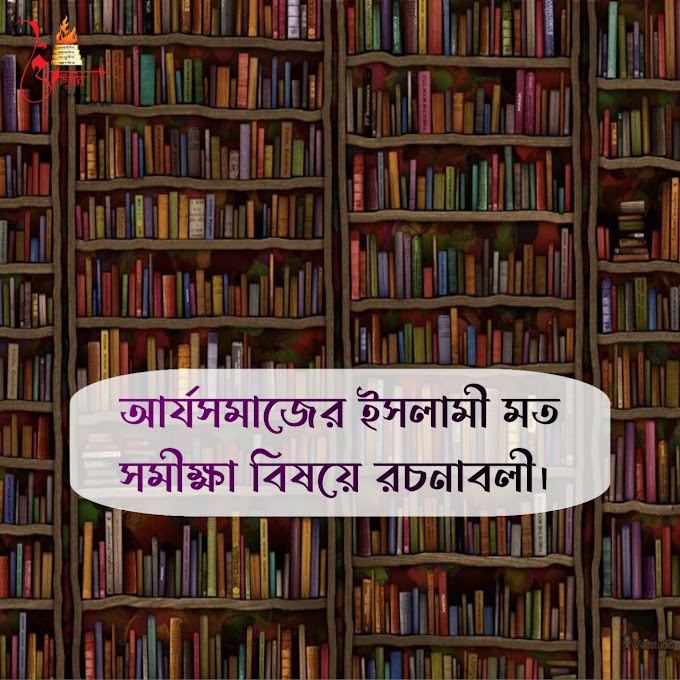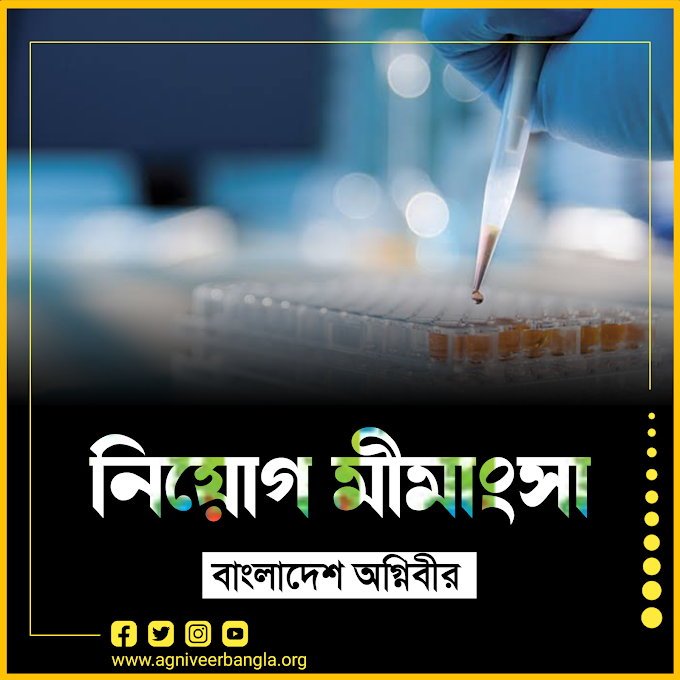উদয়ন, উদয়কর এবং উদ্দ্যোতকর-এঁরা একই ব্যক্তি, একথা কেউ কেউ বলেন। কিন্তু সেই মত ঠিক নয়। কারণ উদয়ন ও উদ্দ্যোতকর –এই উভয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ‘ন্যায়বার্ত্তিক'কার হলেন উদ্দ্যোতকর। ন্যায়বার্ত্তিক এর উপর ন্যায়বার্ত্তিক তাৎপর্যটীকা রচনা করেন ষড়দর্শন টীকাকার বাচস্পতিমিশ্র। আবার ন্যায়বাৰ্ত্তিকতাৎপর্য টীকার উপর ন্যায়বার্তিকতাৎপর্যপরিশুদ্ধি অথবা ন্যায়নিবন্ধ, কিংবা ন্যায়পরিশিষ্ট, কিংবা প্রবোধসিদ্ধি বা বোধসিদ্ধি নামক গ্রন্থ উদয়নাচার্য্য রচনা করেন। এই গ্রন্থের মঙ্গলশ্লোকে বলা হয়েছে -
মাতঃ সরস্বতি পুনঃ পুনরেষ নত্বাবদ্ধাঞ্জলিঃ কিমপি বিজ্ঞাপয়াম্যবেহি।বাক্চেতসোমম তথা ভর সাবধানাবাচস্পর্বেচসি ন স্খলতো যথৈতে।।
তাঁর রচনাবলীর মধ্যেই উল্লেখ পাওয়া যায় যে, তিনি শৈব ছিলেন। এবং তাৎপর্যপরিশুদ্ধির তৃতীয় অধ্যায়ে উদয়ন ‘শ্রীবৎস' নামক এক ন্যায়াচার্যের সন্দর্ভ উদ্ধৃত করেছেন। এর থেকে অনেকে অনুমান করেন যে, এই শ্রীবৎসই উদয়নাচার্যের গুরু ছিলেন।
উদয়নাচার্যকে মিথিলাবাসী বলে আধুনিক গবেষকরা বলেছেন। মিথিলায় দুইটি পরিবার উদয়নের বংশ বলে জানা যায়। এবিষয়ে S.N. Sinha তাঁর 'History of Tirhut' গ্রন্থে (1922, Page-174 fn.) বলেছেন। মিথিলার দারভাঙ্গার উত্তরে প্রায় কুড়ি মাইল দূরবর্তী মনরোণি নামক একটি গ্রামের এক উচ্চবংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন; যা তৎকালীন কমলা নামক নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত। একথা অচার্য্য S.C. Vidyabhusana তাঁর A History of Indian Logic' গ্রন্থে (MLBD Page-142) বলেছেন ।
প্রাচীন ও নব্যন্যায়ের মধ্যবর্তী এই বিখ্যাত নৈয়ায়িক খ্রীষ্টীয় দশম শতকের চতুর্থ পাদে বর্তমান ছিলেন বলে গবেষকদের মত। এবিষয়ে তিনি নিজেই তাঁর ‘লক্ষণাবলী’ গ্রন্থের অন্তিম শ্লোকে বলেছেন -
তর্কাম্বরাঙ্কপ্রমিতেম্বতীতেষু শকান্ততঃ।বর্ষেষুদয়নশ্চক্রে সুবোধাং লক্ষণাবলীম্।।
অর্থাৎ ৯০৬ শকাব্দ কিংবা ৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দে উদয়ন বিদ্যমান ছিলেন তা তিনি নিজেই বলেছেন। যদিও এ বিষয়ে বিশিষ্ট গবেষক অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ভিন্নমত পোষণ করেছেন তাঁর ‘বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা' গ্রন্থে (পৃ. ৫)। এরূপ কথিত আছে যে, একদা ভগবান শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধমত নিরাকরণ করেন। পুনরায় পরবর্তীকালে সেই মত আবির্ভূত হলে আচার্য্য উদয়ন তা নিরাকৃত করেন। পরে তিনি পুরুষোত্তম জগন্নাথধামে গমন করেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে ভগবানের দর্শন তিনি পাননি। তখন স্তবাদিতে পূজা করেও ভগবান যখন দর্শন দিচ্ছেন না, তখন পুরুষোত্তম মন্দির থেকে নির্গত হওয়ার উপক্রম হলে ভগবান তৎক্ষণাৎ উদয়নকে দর্শন দেন ও আচার্য্য তাতে প্রীত হয়েছিলেন।
কেউ কেউ উদয়নাচার্যকে উদয়নভাদুড়ি নামে কোন বারেন্দ্রকুলতিলক বঙ্গীয় বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু তা যথার্থ নয়।
কুসুমাঞ্জলি প্রণেতা আচার্য্য উদয়ন খন্ডনখন্ডখাদ্য কর্তা শ্রীহর্ষের পূর্বকালীন ছিলেন। কারণ, খন্ডন গ্রন্থে শ্রীহর্ষ কুসুমাঞ্জলিস্থিত একটি কারিকাকে উপহাসচ্ছলে কিছু পরিবর্তন করে পাঠ করেন বলে শোনা যায়
শঙ্কা চেদনুমাস্ত্যেব ন চেচ্ছঙ্কা কুতস্তরাম্।ব্যাঘাতাবধিরাশঙ্কা তৰ্কঃ শঙ্কাবধিঃ কুতঃ।।যা কুসুমাঞ্জলিতে এরূপ -শঙ্কা চেদনুমাস্ত্যেব ন চেচ্ছঙ্কা ততস্তরাম্।ব্যাঘাতাবধিরাশঙ্কা তৰ্কঃ শঙ্কাবধিৰ্মতঃ।।
বলাই বাহুল্য বঙ্গীয় ব্রাহ্মণদের বারেন্দ্রাদি শ্রেণীবিভাগ শ্রীহর্ষের পরবর্তী বল্লাল সেনই করেছেন। তাই কিভাবে তার পূর্বে কুসুমাঞ্জলির কর্তা উদয়ন ভাদুড়ির প্রাদুর্ভাব হবে? আবার, কুসুমাঞ্জলিকারের নিজের উক্তিতেই তিনি যে বঙ্গীয় নন, তা বোঝা যায়। তিনি কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে বলেছেন, “ভবতি হি বেদানুকারেণ পঠ্যমানেষু মন্ধাদিবাক্যেষু অপারুষেয়ত্বাভিমানিনী গৌড়মীমাংসকস্যার্থনিশ্চয়ঃ” (৩/১৪)। এখানে ‘গৌড়মীমাংসক' পদের দ্বারা প্রকরণপঞ্চিকাকার শালিকনাথ বঙ্গীয় লক্ষিত হয়। এটি 'কুসুমাঞ্জলিবোধনী’তে বরদরাজের ব্যাখ্যায় উপলব্ধ হয়।
আবার সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীর ভূমিকায় মহামহোপাধ্যায় তারানাথ তর্কবাচস্পতি বাচস্পতিমিশ্রকৃত খন্ডনোদ্ধারকে দেখে খন্ডনোদ্ধারকার বাচস্পতিমিশ্র ও সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীকার বাচস্পতিমিশ্রকে অভিন্ন মনে করেন। এবং তাতে খন্ডন কার শ্রীহর্ষ সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী প্রণেতা বাচস্পতি মিশ্রের পূর্বভারী ছিলেন এটি যে উল্লিখিত আছে, তা সঠিক নয়। কারণ, খন্ডনোদ্ধারকার নব্য বাচস্পতি ষড়দর্শনটীকাকার বাচস্পতি থেকে ভিন্নই—একথা তাদের উভয়ের গ্রন্থালোচনা থেকেই বোঝা যায়। উদয়নাচার্যের থেকে প্রাচীনতর ইনি শ্রীহর্ষ থেকে প্রাচীন কোনভাবেই হতে পারেন না।
বৌদ্ধদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধ বিষয়ে উদয়নের সম্বন্ধে অনেক প্রচলিত প্রবাদ উল্লিখিত রয়েছে। একসময় ঐরকম এক বিবাদ চলাকালীন ঈশ্বর আছে কি নেই এই বিষয়ে বৌদ্ধদের সঙ্গে চূড়ান্ত তর্কযুদ্ধ শুরু হয়। কোনভাবেই বৌদ্ধ ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানছেন না। তাই উদয়ন একটি বুদ্ধি করলেন। একটি পাহাড়ের চূড়ায় এক ব্রাহ্মণ ও এক শ্রমণ (বৌদ্ধ) কে নিয়ে উঠে গেলেন। তিনি ঐ দুজনকে চূড়া থেকে গড়িয়ে দিলেন এবং যখন নিচের দিকে গড়াচ্ছে তখন ঐ ব্রাহ্মণটি চিৎকার করে কাঁদছে ও বলছে ঈশ্বর আছে'। আর শ্রমণটি বলছে, 'ঈশ্বর নেই। ফলে শেষ পর্যন্ত শ্রমণ মারা যায় এবং ব্রাহ্মণ নিচ পর্যন্ত জীবিত ফিরে আসে। এই ঘটনা অংশতঃ প্রমাণ করে যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব রয়েছে ও তা প্রমাণসিদ্ধ। এর পরের ঘটনা হ’ল তাঁর পুরীধাম যাত্রা ও পুরুষোত্তম শ্রীজগন্নাথদর্শন।
আচার্য্য উদয়ন এতই বিখ্যাত ছিলেন যে, তাঁর সম্বন্ধে পুরাণে ও অনেক কাহিনী পাওয়া যায়। এমনই কিছু কথা পাওয়া যায় ‘ভবিষ্যপুরাণে'র পরিশিষ্ট পর্বে তিরিশতম অধ্যায়ে -
অথ বক্ষ্যে তৃতীয়স্য হরেরংশস্য ধীমতঃ।উদয়নাচার্য্যনাম্নত্ত মাহাত্ম্যং লোমহর্ষণম্।। ১।ভূত্বা স মিথিলায়াং তু শাস্ত্রাণ্যধ্যৈষ্ট সর্বশঃ।বিশেষতো ন্যায়শাস্ত্রে সাক্ষাদ্বৈ গৌতমো মুনিঃ।। ২।বৌদ্ধসিদ্ধান্তমুগ্ধান্তঃ, সুখায় হিতকারিণীম্।বিতেনে বিদুষাং প্রীত্যৈ বিমলাং কিরণাবলীম্। ৩।।
ভারতীয় দর্শনাকাশে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক আচার্য উদয়ন একাধারে যেমন প্রতিষ্ঠিত নৈয়ায়িক ছিলেন তেমন বৈশেষিকদর্শনেও ছিল তাঁর প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি। শুধু তাই নয়, প্রমাণশাস্ত্র হিসেবে নব্যন্যায়েরও আদি ও যুগস্রষ্টা আচার্য। অসাধারণ তার্কিক এই মহান্ দার্শনিক বৌদ্ধদার্শনিকদের কাছেও অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। ফলে সংক্ষেপে তাঁর বিদ্যাবত্তার পরিচয় দেওয়া খুবই কঠিন। তা সত্ত্বেও আধুনিক গবেষকরা তাঁর রচনাবলীর সম্বন্ধে এরূপ বলেছেন যে, উদয়নের রচনাকে প্রথমতঃ দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এক শ্রেণীর হ’ল মৌলিক রচনা ও অপর শ্রেণীর হল টীকা গ্রন্থ। টীকা সমূহের মধ্যে :
- ক) মহর্ষি গৌতমের সূত্রের উপর ‘ন্যায়পরিশিষ্ট' যা ন্যায় সূত্রের দুরূহতম অংশ পঞ্চমাধ্যায়ের উপর প্রবোধসিদ্ধি নামেও পরিচিত। এটি বর্দ্ধমানোপাধ্যায়ের ‘পরিশিষ্টপ্রকাশ' সহ মুদ্রিতাকারে পাওয়া যায়।
- খ) আচার্য প্রশস্তপাদের ‘পদার্থধর্মসংগ্রহ' গ্রন্থের টীকা কিরণাবলী। এটি অত্যন্ত দুরূহ গ্রন্থ। অনেকের মতে এই গ্রন্থটি উদয়নাচার্যের শেষ গ্রন্থ। এখানে আত্মতত্ত্ববিবেক ও ন্যায়কুসুমাঞ্জলি'র কিছু কিছু উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। এটি নানা ব্যাখ্যাসহ মুদ্রিত হয়েছে।
- গ) বাচস্পতিমিশ্রের 'ন্যায়বার্ত্তিক তাৎপর্যটীকা'র অবলম্বনে ‘ন্যায়বার্ষিক তাৎপর্যপরিশুদ্ধি’ অথবা ‘ন্যায়নিবন্ধ’। গ্রন্থটি বর্দ্ধমানের ‘প্রকাশ’ টীকা সহ পাওয়া যায়।