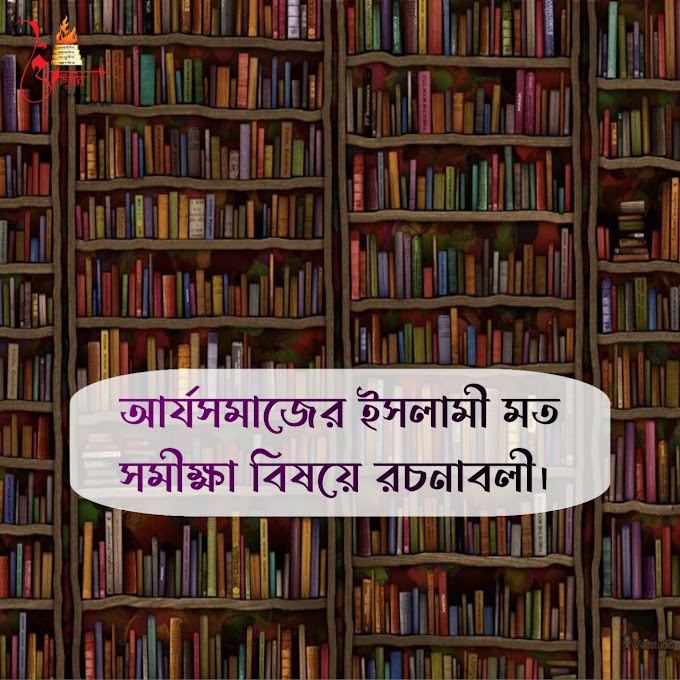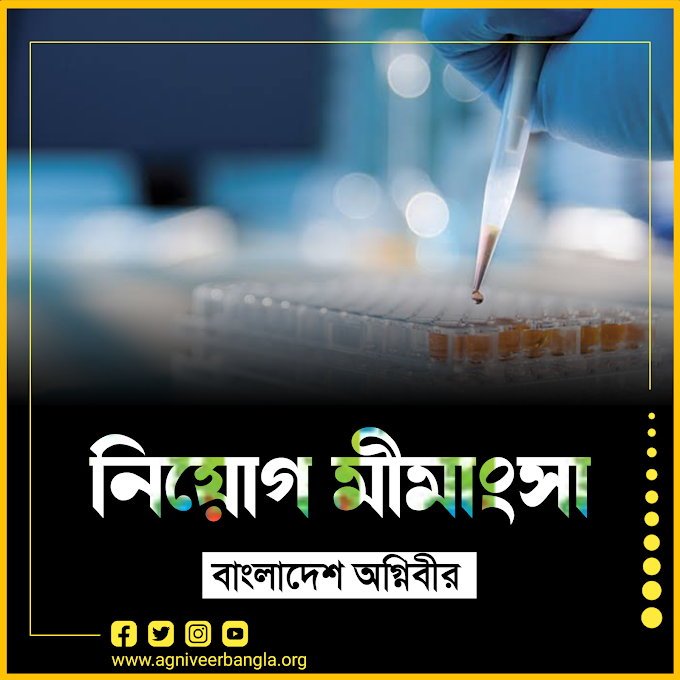॥ও৩ম্॥
ভগবৎপাদ্ মহর্ষি শ্রীমৎ দয়ানন্দ সরস্বতী মহারাজ ভারতবর্ষের ভাগ্যাকাশে এক স্মরণীয় ধ্রুবতারার নাম। তিনি বৈদিক যুগের মুনি-ঋষিদের আবিস্কৃত অভ্রান্ত নৈরুক্তিক বা আর্ষ পদ্ধতিতে নিরূপিত বেদার্থের সাথে বিশ্ববাসীকে পুনরায় তাঁর বেদভাষ্যের মাধ্যমে পরিচিত করেছিলেন। তাঁর এই মহান প্রয়াসের ফলে বেদার্থ মধ্যযুগীয় ও আধুনিক ইউরোপীয় এবং তদনুসারী কথিত ভারতীয় পণ্ডিতদের ভ্রান্ত ধারণা থেকে রক্ষা পেয়ে সত্যস্বরূপে প্রকাশিত হতে থাকে। আজকের লেখায় ঋষির বেদসাধনার সম্পূর্ণ ইতিহাস তুলে ধরা হবে।
যার পুরো জীবনই বেদাধারিত ছিল তাঁর বেদসাধনার সম্পূর্ণ ইতিহাস বর্ণনা করা অসম্ভব। তাই তাঁর বেদসাধনার যতটুকু নমুনা সাহিত্যাকারে আমরা পেয়েছি শুধুমাত্র সে প্রসঙ্গেই প্রামাণিক তথ্য উপস্থাপন করব। লেখার শুরুতেই কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি মহামহোপাধ্যায় আচার্য পণ্ডিত যুধিষ্ঠির মীমাংসকজী ও আর্ষসাহিত্য প্রচার ট্রাস্টের পণ্ডিতদের যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই ইতিহাস আমাদের জন্য সুলভ হয়েছে।
ঋষির বেদার্থ প্রকাশরূপ বা বেদভাষ্যরূপ সাহিত্য হিসেবে আমরা নিচের গ্রন্থগুলোর নাম উল্লেখ করতে পারি-
পূর্বার্ধে প্রধানত বেদ, ব্রাহ্মণ গ্রন্থ, উপনিষদ্, ষড়দর্শন, মনুস্মৃতি ইত্যাদি প্রাচীন আর্ষগ্রন্থের আধারে বৈদিক ধর্মের মূখ্য মূখ্য সিদ্ধান্তের বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং উত্তরার্ধে ক্রমশঃ পৌরাণিক, তান্ত্রিক, গুরুবাদী সম্প্রদায়, চার্বাক, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্ট এবং ইসলাম মতবাদের সমালোচনা করা হয়েছে। সর্বশেষে মহর্ষি স্বমন্তব্যামন্তব্যপ্রকাশ অংশে বৈদিক ধর্মের মূলভুত সিদ্ধান্ত সংক্ষিপ্ত সূত্ররূপে উপস্থাপন করেছেন।
কাশীতে ১৯৩১ বিক্রমাব্দের ১১ই আষাঢ় (১২ জুন ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দ) শুক্রবারে ঋষি সত্যার্থ প্রকাশ লেখানোর কাজ শুরু করেন। মহর্ষি ধারাবাহিকভাবে বলতেন আর মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত চন্দ্রশেখর লিখতে থাকতেন। গ্রন্থ রচনার কাজ ৬ মাসের মধ্যেই সমাপ্ত হয়ে যায়।
ঋষি দয়ানন্দ এই গ্রন্থের সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯ আগষ্ট ১৮৮২ (বিক্রম সম্বত ১৯৩৯) থেকে ২৯ ডিসেম্বর ১৮৮৩ (বিক্রম সম্বত ১৯৪০) পর্যন্ত প্রেসে সংশোধন করে দিতে থাকেন। কিন্তু সংশোধনের সম্পূর্ণ কাজ শেষ করার আগেই অকালে তাঁর ইহলোক ত্যাগের কারণে শেষের কিছু অংশ (মুদ্রণকপি ৩৪৫-৪৯৮ পৃষ্ঠা) অসংশোধিত অবস্থায়ই থেকে যায় এবং সে অবস্থায়ই প্রকাশিত হতে থাকে। এর প্রকাশনা শুরু হয় ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে এবং ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে তা সম্পূর্ণ হয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত হয়।
প্রথমবার সত্যার্থ প্রকাশ রচনার পর পরপরই চার বেদের ভাষ্য করার আবশ্যকতা অনুভব হয় মহর্ষির। কারণ বৈদিক ধর্মের যে ব্যাখ্যা ঋষি সত্যার্থ প্রকাশের পূর্বার্ধের ১০ সমুল্লাসে করেছেন তার মূখ্য আধার ছিল বেদ। তিনি ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে ভারতবর্ষে ধার্মিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবনতির মূখ্য কারণ বৈদিক শিক্ষার লোপ ও পৌরাণিক শিক্ষার প্রসার। এমনকি সেসময় বেদের ভাষ্য বা টীকা হিসেবে প্রচলিত সায়ণ, মহীধর, উবটের টীকাসমূহের রচয়িতাদের মস্তিষ্কে পৌরাণিক যুগ ও সেই শিক্ষার অত্যাধিক প্রভাব ছিল। একারণে তারা প্রাচীন আর্ষগ্রন্থবিরুদ্ধ অত্যন্ত ভ্রষ্ট ও যুক্তিবিরুদ্ধ ব্যাখ্যান করে বেদকে কলুষিত করেছিলেন। এই মধ্যযুগী টীকায় পৌরাণিক শিক্ষা-দীক্ষা, আচার ব্যবহার এবং মান্যতাকে প্রামাণিকতার এমন মোহরাঙ্কিত করেছিল যাতে সর্বসাধারণ তো দূর অনেক বড় বড় পণ্ডিতেরাও তার বিরুদ্ধে কিছু বলার সাহস পাননি। কিন্তু কোথায় প্রাচীন আর্ষ গ্রন্থে বর্ণিত বৈদিক ধর্মের পরমোদাত্ত সিদ্ধান্ত আর কোথায় বেদের এসব অনর্থকারী টীকা।
ঋষি সকল প্রাচীন আর্ষ গ্রন্থ দ্বারা বৈদিক ধর্মের গূঢ় রহস্য ও সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করে তদনুসারে বেদ ও সকল নবীন টীকা অনুশীলন করে উপলব্ধি করেন যে বেদের বাস্তবিক শুদ্ধ স্বরূপকে কলুষিত করেছে এইসকল নবীন টীকা-ভাষ্য। এইকারণে তিনি বৈদিক শিক্ষা তথা আচার-বিচার পুনরুদ্ধারের জন্য প্রাচীন আর্ষ পদ্ধতি অনুসারে বেদভাষ্য করার সংকল্প করেন এবং সে কাজের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা শুরু করেন। ঋষি দয়ানন্দ বেদভাষ্য করার সংকল্প নিয়েছিলেন বিক্রম সম্বত ১৯২৯ এর অন্ত বা ১৯৩০ এর শুরুতে।
অসীম সাহসী দোর্দণ্ডপ্রতাপ পরমবিদ্বান ঋষি সত্যের বলে বলীয়ান হয়ে বজ্রকণ্ঠে এই নমুনার ভূমিকায় ঘোষণা করলেন-
“আমি এই শৈলীতে সম্পূর্ণ বেদের ভাষ্য করব। যদি কারো এই পদ্ধতিতে আপত্তি থাকে তবে প্রথমেই তা প্রদর্শন করুন, তার খণ্ডন করার পরই ভাষ্য শুরু করব।” [তথ্যসূত্রঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়]
ঋষি ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে রাজা জয়কৃষ্ণদাসের মাধ্যমে তাঁর এই নমুনা ভাষ্য কাশীর পণ্ডিত বালশাস্ত্রী, স্বামী বিশুদ্ধানন্দ, কলকাতার শ্রী কে. এম. ব্যানার্জি (বালীগঞ্জ), শ্রী রাজেন্দ্রলাল মিত্র (মানিকটোলা), অমৃতসরের শ্রী দয়ালসিংহ মজীঠিয়া এবং ভারতবর্ষের অন্যস্থানের পণ্ডিতদের কাছেও পাঠান। নাম উল্লেখ করা পণ্ডিতগণ ক্রমশ ১০ ডিসেম্বর, ১১ ডিসেম্বর, ২৬ ডিসেম্বর ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে রাজা জয়কৃষ্ণদাসের নিকট সম্মতিপত্র পাঠান।
এ সময় ঋষি বোম্বাই নগরে ছিলেন। এই নমুনা ১৯৩১ বিক্রমাব্দেই রচিত হয়েছিল। আচার্য যুধিষ্ঠির মীমাংসকজী লিখেছেন- “এই নমুনাভাষ্য আমরা দেখতে পাইনি। এর নির্দেশ বিক্রম সম্বত ১৯৩২ এ প্রকাশিত বেদান্তিধ্বান্তনিবারণ পুস্তকের শেষের বিজ্ঞাপনে দেখা যায়।” অর্থাৎ সংরক্ষণের অভাবে এই নমুনাভাষ্যটি সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গেছে।
ঋষি এই গ্রন্থের ভূমিকায় লেখেন-
“এই গ্রন্থ থেকে কেবল মানুষের ঈশ্বরের স্বরূপজ্ঞান, ভক্তি, ধর্মনিষ্ঠা, ব্যবহারশুদ্ধি এইসকল প্রয়োজন সিদ্ধ হবে। যাতে নাস্তিক্যমত ও পাখণ্ডমতাদি অধর্মে মানুষ লিপ্ত হবেনা।”“ঈশ্বরের স্তুতি-প্রার্থনা-উপাসনা করার নিমিত্তেই বেদমন্ত্রের সমাবেশ নিয়ে এই পুস্তক তৈরি করা হয়েছে।”
১৯৩২ বিক্রমাব্দের চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের দশমী তিথি গুরুবারে পুস্তকটির রচনা শুরু হয়। এতে ঋগ্বেদের ৫৩টি, যজুর্বেদের ৫৪টি মন্ত্র ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ১টি সহ মোট ১০৮ মন্ত্রের ব্যাখ্যান রয়েছে। আচার্য যুধিষ্ঠির মীমাংসকজীর মতে ঋষির এই গ্রন্থটি অসম্পূর্ণ। তিনি বলছেন এই গ্রন্থে ঋষি মোট ৬ অধ্যায় লিখতে চেয়েছেন যার প্রথম দুই অধ্যায় সম্পন্ন হয়েছে বাকি সামবেদ, অথর্ববেদ, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ এর মন্ত্রের ব্যাখ্যা লেখা অপূর্ণ রয়ে গেছে। তিনি ১৯৩২ বিক্রমাব্দে শ্রী গোপালরাও হরিদেশমুখকে লেখা ঋষির এক পত্র থেকে প্রমাণ উল্লেখ করেন যেখানে ঋষি বলছেন-
“আর্য্যাভিবিনয় এর দুই অধ্যায় তৈরি হয়ে গেছে, পরবর্তীতে আরো চার অধ্যায় লেখা হবে।”
গ্রন্থের উপক্রমণিকার ৫ম শ্লোককেও তিনি প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেন যেখানে লেখা আছে -
“এই গ্রন্থে কেবল চার বেদ ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থের মূল মন্ত্রের প্রাকৃত ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে।”
অতএব, গ্রন্থটি অসম্পূর্ণই বলা যায়। কিন্তু কেন এটি ঋষি আর সম্পন্ন করেননি তা জানা যায়না। সম্ভবত প্রচার ও বেদভাষ্য রচনার কাজে ব্যস্ত থাকার জন্যই এই কাজ আর সম্পূর্ণ করা হয়নি।
আর্য্যাভিবিনয় এর প্রথম সংস্করণ ১৯৩২ বিক্রমাব্দে ছাপানো হয়। পরবর্তীতে ঋষি এর ভাষাগত সংশোধন করে দ্বিতীয় সংস্করণও বের করেন। গ্রন্থটি আর্যভাষা হিন্দিতে রচিত।
১৯৩২ বিক্রমাব্দের পরে ঋষি বেদভাষ্যের কাজকে এতটা গুরুত্ব দেন যে তিনি নিজের পারমার্থিক প্রযত্নতেও শিখিলতা দেখান এবং নিজেকে সর্বোপরি উজার করে দিয়ে কাজে লাগেন। ঋষি তাঁর এক পত্রে উল্লেখ করেন- “আমি কেবল পরমার্থ ও স্বদেশোন্নতির নিমিত্তে নিজের সমাধি ও ব্রহ্মানন্দ ছেড়ে বেদভাষ্যের কাজ গ্রহণ করেছি।”
এই নমুনায় বেদে প্রযুক্ত অগ্নি, বায়ু ইত্যাদি শব্দ যে ঈশ্বরবাচক তা প্রমাণ করতে বেদ থেকে শুরু করে মৈত্রায়নী উপনিষদ্ পর্যন্ত অনেক আর্ষ গ্রন্থের প্রমাণ দেয়া হয়েছিল। ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকায় এই নমুনাভাষ্যেরই উল্লেখ করা হয়েছে এবং এটি বর্তমানে উপলব্ধ। আলাদা দুটো পুস্তিকা আকারে বর্তমানে এই নমুনাঙ্ক উপলব্ধ।
মুলত পণ্ডিত মহেশচন্দ্র, গোবিন্দরাম - ঋষির ভাষ্যের উপরে আক্ষেপ করে বই লেখেন এবং শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী এর খণ্ডনে কিছু লেখা এক প্রবন্ধ আকারে নিজের পত্রিকা (বিরাদরে হিন্দ)-এ এবং ‘দয়ানন্দ সরস্বতীর বেদভাষ্যের রিভিউ’ নামে এক পৃথক পুস্তক প্রকাশ করেন। মহেশচন্দ্রের পুস্তক সবার শেষে বেরোয় এবং এতে আগের সব পণ্ডিতদের আক্ষেপগুলো একত্রে থাকায় ঋষি এই বইটিরই খণ্ডন করে ভ্রান্তিনিবারণ নামক পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তক লঘু হলেও বেদার্থ-জিজ্ঞাসুদের কাছে এ এক রত্নস্বরূপ।
ঋগ্বেদের সাথে সাথেই এই ভাষ্য নির্মাণও চলতে থাকে এবং ঋগ্বেদ ভাষ্যের সাথে সাথে এই ভাষ্যও প্রকাশিত হতে থাকে। ঋষি তাঁর জীবনকালে সসম্পূর্ণ যজুর্বেদের ভাষ্য করেন।
বেদভাষ্যের সম্পূর্ণ কাজ ঋষি সংস্কৃত ভাষায় করেন। এর ভাষ্যানুবাদ তাঁর সহকারী পণ্ডিতগণ করেন একারণে কিছু কিছু স্থানে ভাষ্যানুবাদ সংস্কৃতের অনুকূল ছিল না।
ঋষি দয়ানন্দের পত্রে এ বিষয়ে উল্লেখ পাওয়া যায়-
১. “ভীমসেন কিছু কিছু অর্থ ছেড়ে গেছে, কিছু অন্বয় ছেড়ে গেছে, কিছু স্থানে শব্দ আগে পিছে করেছে।”
২. “কিছু স্থানে জ্বালাদত্ত সংস্কৃত থেকে ভিন্ন ভাষা বানিয়ে দিয়েছে... তা যদি এভাবে প্রকাশিত হয় তবে বড় হানিকর কাজ হবে।”
৩. “কিছু স্থানে পদার্থ একরকম আর ভাষা অন্যরকম করেছে।”
ঋষি দয়ানন্দ ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ৮৬ সূক্তের ৫ম মন্ত্র পর্যন্ত ও যজুর্বেদের ১৫ অধ্যায়ের ১৬ মন্ত্র পর্যন্ত নিজের হাতে সংশোধন করেন।
দেরিতে হলেও পরবর্তীতে ঋষি দয়ানন্দের যজুর্বেদের সংস্কৃত ভাষ্য মূল হস্তলেখ অনুযায়ী সংশোধন ও মূলানুযায়ী বিশুদ্ধ হিন্দি অনুবাদ করেন আচার্য সুদর্শনদেবজী এবং ঋগ্বেদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ কাজ করেন আচার্য সুদর্শনদেবজী ও পণ্ডিত শ্রী রাজবীর শাস্ত্রীজী। এই মহান কর্মযজ্ঞ বর্তমানে ঋগ্বেদ ভাষ্য ভাষ্কর ও যজুর্বেদ ভাষ্য ভাষ্কর নামে আর্য সাহিত্য প্রচার ট্রাস্ট, দিল্লি থেকে প্রকাশিত হয়।
ঋষির শৈলীতে ঋগ্বেদের বাকি অংশের ভাষ্য করেছেন আর্য জগতের তিন খ্যাতিমান বিদ্বান (১) মহামহোপাধ্যায় আচার্য আর্যমুনিজী, (২) আচার্য শিবশঙ্কর শর্মাজী কাব্যতীর্থ, (৩) স্বামী ব্রহ্মমুনি পরিব্রাজকজী।
সামবেদ ও অথর্ববেদের ক্ষেত্রে অনুরূপ কাজ করেন যথাক্রমে আচার্য রামনাথ বেদালঙ্কারজী ও আচার্য ক্ষেমকরণ দাস ত্রিবেদীজী।
ঋষির দেখানো পথে বেদার্থ পুনরায় তার পূর্বস্বরূপ ফিরে পায় একইসাথে হাজারো কলুষতা থেকে মুক্ত হয়। সত্য সনাতন ধর্ম দৃঢ়ভিত্তিতে স্থাপিত হয়।
তথ্যসূত্রঃ
১. ঋষি দয়ানন্দ কে গ্রন্থোং কা ইতিহাস - আচার্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যুধিষ্ঠির মীমাংসকজী
২. আর্ষ সাহিত্য প্রচার ট্রাস্ট দ্বারা প্রকাশিত ঋষি দয়ানন্দের গ্রন্থের ভূমিকাসমূহ
-ইত্যোম্